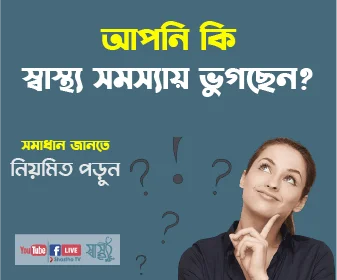কারাগারের সাধারণ বন্দীদের জীবন যাপনের মান নিয়ে একটু কথা বলা প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। খাবারের ব্যাপারে প্রথমে আসি। আমাদের মতো বন্দীদের খাবার আলাদা আসতো,সাধারণ বন্দীদের খাবারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু আমরা তো কখনো একজন,কখনো বা দুইজন। কারাগারের সাধারণ বন্দীদের সকালের খাবার ছিলো রুটির মতো দেখতে একটা কিছু। সেই রুটিতে লেপটে দেওয়া হোতো গুড়ের মতো দেখতে আর একটা বিশেষ কিছু। আমি হলফ ক’রে বলছি সকালে এর থেকে বেশি কিছু নয়। অথচ ঐরকম তিনটা রুটি হলে কিছুটা ঠিক হোতো। বলা যেতো সকালের খাবার দেওয়া হচ্ছে। আমার চোখে খাবারের নামে তা ছিলো প্রহসন। এখানে বাচ্চাদের কথা আমি বলছিনা। দুপুরে বড় বড় হাড়ি বা ডেক বাঁশে ঝুলিয়ে আনতো পুরুষ বন্দীরা। সকালের খাবারও বাইরে থেকে পুরুষ বন্দীরাই দিয়ে আসতেন। দুপুরের তরকারী মানে মুলো যখন পাওয়া যায়,তখন মুলোই চলতো। বেগুন বা মিষ্টি কুমড়ো যখন পাওয়া যেতো,তখন ঐটাই চলতো দিনের পর দিন। যেন বাজারে আর কিছু পাওয়া যায় না। আর তরকারীর চেহারা দেখে মনে হোতো ড্রেনের কাদা মাটির সঙ্গে হলুদ লবন মিশানো একটা কিছু। কারাগারে যারা থাকে,ধরেই নেওয়া হয় এরা অপরাধী। এরা মানুষ না। অতএব শুরু থেকেই যতো পারো শাস্তি দাও আর নির্যাতন করো। এটাই আমাদের দেশের কারাগারের চিত্র।
রাতের খাবার দেওয়া হোতো বিকালে। আলাদা কোনো মেনু নয়। দুপুরের বেচে যাওয়া খাবারই রাতে দেওয়া হোতো অথবা দুই বেলারটা একবারে রান্না করা হোতো। কারণ একই জিনিস দেখতাম। আর আমি আজও আবিষ্কার করতে পারিনি এই ব্যবস্থা কেন। রাতের খাবার বিকালে কেন! ব্রিটিশ আমলের নিয়ম এটা। ব্রিটিশরা আমাদের মানুষ মনে করতোই না। তাদের হিসাব ছিলো যতো পারো এদের জন্তু বানিয়ে রাখো আর খাটিয়ে নাও। সেই খাটিয়ে নেওয়া এবং আমার ধারণা বিদ্যুৎ স্বল্পতার কারনে কারাগারে উদয়াস্তের নিয়ম ছিলো। কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশে কেন কারাবন্দীদের জন্য এই নিয়ম থাকবে,এটা ভেবে বের করা কঠিন। এখন বিদ্যুতের আলোয় তো রাতকে দিন বানিয়ে দেওয়া যায়। তাছাড়া এখনো কেন দাসের মতোই দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে ব্রিটিশের মতো। ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাবে লেখা থাকতো কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিশেধ। এখন তো সেখানে তা লেখা নেই। তাহলে কারাগারে কেন ব্রিটিশের উদয়াস্ত আইন থাকবে। বিকালে রাতের জন্য বন্দীদের যে খাবার দেওয়া হোতো,প্রায়ই দেখতাম অনেকের খাবারয়ই নষ্ট হয়ে যেতো। কেউ কেউ সেই বিকালেই খেয়ে নিতো। সেও এক বিড়ম্বনা। তাছাড়া এ কতোবড় নির্যাতন ভাবা যায়? আমার এখনো মনে হয় আমাদের দেশের এক শ্রেণির মানুষের মাথায় গোবর আছে। নইলে এই সহজ কথাটা তারা কেন বোঝেনা রাতেই বন্দীদের খাওয়া দাওয়া করিয়ে দিব্যি তালা দিয়ে চলে যাওয়া যায়। অবশ্য তার আগে মানতে হবে কারাগারে যারা থাকে তারাও মানুষ। আমাদের দেশে একশ্রেণীর অলস এবং শয়তান প্রকৃতির লোকজন বসে আছে আমাদের জায়গায় জায়গায়। ওরা জুতার কারখানায় বসে জুতার মাপে পা কেটে জুতা বানিয়ে চলেছে। আর তার খেসারৎ দিচ্ছি আমরা-আমজনতা। সুবেদার সাহেব সন্ধ্যায় ওয়ার্ডে তালা দিয়ে চাবি নিয়ে চলে যান। ওয়ার্ডের সঙ্গেই সেল। সেল আমার থাকবার জায়গা। আমি ইচ্ছা করলে রাতেও সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। তারপরেও তালাবদ্ধ ঘরে মনে হোতো এ রাত বুঝি আর শেষ হবে না। সারারাত আমার মাথার উপরে জ্বলতো ১০০ পাওয়ারের লাইট। রাতে জেলখানাটা মনে হোতো যেন মশার রাজ্য। সে একটা দুইটা মশা নয়। তার সংখ্যা যে কতো,তা যে জেল খেটেছে সেই বুঝতে পারবে। জেলখানায় ঢুকে গরমের সঙ্গে নতুন ক’রে পরিচয় হোলো। আমি গ্রামের মেয়ে। বড় হয়েছি বিদ্যুৎ ছাড়া। তারপরেও আমার কাছেও জেলখানার গরম মনে হোতো যেন ঝলসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কীভাবে যে সুস্থ শরীর নিয়ে জেল থেকে বের হয় তা ভেবে আমি আজও বের করতে পারিনি। আর শীতের ব্যাপারে শুনেছি,গায়ে দেওয়ার জন্য পাতলা সেই ৭১ সালের রিলিফের কম্বল,আর মাথার নিচে দেওয়ার জন্য একটা কম্বল দেওয়া হয়। মেঝে তো পাকা। এখন সেই দুটো কম্বল হাতে ক’রে শীতের সময় বন্দীরা সব দাঁড়িয়ে থাকে,নাকি বসে বসে রাত পার করে তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। কনকনে শীতে,পাকা মেঝেতে দুটো পাতলা রিলিফের কম্বল নিয়ে তারা কী করবে! কারাগারে বন্দীদের জন্য আরও তৈরি ক’রে রাখা আছে নির্যাতনের নানান ধরণের ফাঁদ। আরও সব অদ্ভুত ধরণের বিড়ম্বনা আছে সেখানে। বন্দী গণনার নিয়ম আছে রাতে। রাত দশটার পর বা এর আগে পরে থেকে শুরু হোতো গুনতি। বাইরে থেকে হাঁক দিলেই চিৎকার ক’রে ভিতর থেকে বলা হোতো ঠিক আছে ২৮০ বা যে সংখ্যা তাই। কিছুক্ষন পর পরই চলতো এই চিৎকার এবং তা সারারাত ধরে। এসব জায়গায় কোন হৃদ রোগীর এক সপ্তার বেশি বাঁচবার কথা নয়। এছাড়া সাধারণ বন্দীদের সকাল সন্ধ্যায় গণনা করা হোতো। যাকে বলা হোতো ফাইল। সন্ধ্যার ব্যাপারটা যদিও বা মেনে নেওয়া যেতো, কিন্তু কাক ভোরে ঘুম থেকে তুলে লোটা কম্বল নিয়ে বসিয়ে যে গণনা করা হোতো,সে নিয়মকে যে কোনো নির্যাতনের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। দুইবারই সুবেদার সাহেবের উপস্থিতিতে এই গণনা করা হোতো। আর একটা দুঃখজনক ঘটনা এখানে আমি বলতে চাই। কারাগারের বন্দীদের সারাদিন খাটানো হোতো অনেকটা দাসের মতো ক’রে। সারাদিন খেটে খুটে বন্দীরা যে একটু গায়ে পানি ঢালবে,সে ছিলো নির্যাতনের আর একটা ধরণ। অত খাটনির পর স্নান করাটা ঘুমের মতোই ছিলো প্রয়োজনীয় বিষয়। অথচ এ দুটোর কোনোটাই বন্দীদের জন্য বরাদ্দ ছিলো না। খাওয়ার কথা তো বলেছিই। বন্দী ২৫০ থেকে ৩৫০ ওঠানামা করতো। টিউবওয়েল একটা। স্নানের সময় এক ঘণ্টা। গোসলের সময় যে দৃশ্যের অবতারণা হোতো, তা মধ্যযুগের দাস ব্যবস্থা কেও হার মানায়। জেলখানার মধ্যে ভাত পানি খাওয়ার জন্য অদ্ভুত থালা বাটি আছে। সেই বাটি নিয়ে বন্দীরা যেতো গোসল করতে। কেউ তিন বাটি থেকে চার বাটি পেয়েছে কিনা আমার তা জানা নেই। সে যে কী নির্মম দৃশ্য! তা বোঝানো খুবই কঠিন। আমি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের অবস্থা তুলে ধরলাম। নারী বন্দীদের জন্য সারা দেশের কারাগারে নিশ্চয় একই ব্যবস্থা। চোখের সামনে এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো। এক বুধবারে ভিজিটে আসা কর্মকর্তাদের শেষপর্যন্ত সমস্যার কথা আমি জানিয়েছি। অবশ্য আমাদের মতো বন্দীদের গোসল করা নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিলো না। আমরা আমাদের নিয়ম মতোই সময় নিয়ে গোসল করবার অধিকার রাখতাম। সমস্যার কথা ডি আই জি সাহেব সহ জেলর সাহেব শুনলেন। এবং বললেন,আর একটা পানির কল্ দরকারও। কাল পরশু আর একটা কল্ বসিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই কাল পরশু আর আসছিলো না। অবশেষে হাঙ্গামা একটু করতেই হোলো। প্রতিবাদ হিসেবে সকলে মিলে একদিন দুপুরের খাবার ফেরত দেওয়া হোলো। এবং জানানো হোলো পানির কলের নিষ্পত্তি না হলে এভাবেই চলতে থাকবে। জেলখানায় এই পদ্ধতির বাইরে প্রতিবাদ করবার আর কোনো কৌশল ছিলো না। সন্ধ্যা বেলায় সুবেদার সাহেব জানিয়ে দিয়ে গেলেন কাল সকালেই টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া হবে। বাড়তি আর একটা কথা বলে গেলেন তিনি। এবার শীতের সময় কম্বলের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন অনেক গরম ছিলো। তাই আমাদের দিক থেকে কম্বলের কথা তখনো বলা হয়নি। আমরা সুবেদার সাহবের কথা বিশ্বাসই করেছিলাম। এবং পরদিন সকালে সত্যিই আর একটা টিউবওয়েল মহিলা ওয়ার্ডে বসিয়ে দেওয়া হোলো।
আমার সঙ্গে বাড়ির যোগাযোগ বন্ধ হয়েই আছে। মাত্র দু’বার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। টিউবওয়েল বসানোর পরপরই আমার সঙ্গে আবার সাধারণ বন্দীদের কথা বলা বন্ধ ক’রে দেওয়া হোলো। এটা হয়েছিলো উপরের নির্দেশে। আমার তখন একমাত্র সম্বল আমাকে দেখাশোনা করা মাজেদা। ততদিনে মেট্রনের সঙ্গেও আমার আন্তরিকতা বেড়েছে। মেট্রন বললেন,কিছুদিন পর আবার আগের মতোই পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে। হাসতে হাসতে তিনি আবার বললেন,আপনারও দোষ আছে। সব সময় একটা না একটা ঝামেলা বাঁধাবেন। তবে এবার বাচ্চাদের আমার কাছে আসা বন্ধ হোলো না। ওদের উপর কোনো বিধি নিষেধ দেওয়া হয়নি। তাছাড়া মেট্রনের দিক থেকে এবার কোনো কড়াকড়ি ছিলো না। তাই আমার এবারের অবসর কাটছিলো বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারাই এখন আমার সব সময়ের সঙ্গী। এই সকল বাচ্চাদের মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই। জেলখানার চার দেয়ালের মধ্যেই ওরা বেড়ে উঠেছে। ওরা অনেকটা সরল বন্য প্রাণীর মতো। শুধু কথা বলতে পারে এই যা। বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে চলার আনন্দই আলাদা। ওদের সঙ্গেই খেলে গল্প ক’রে তখন সময় কাটাতাম। একদিন বুলু নামের ৬/৭ বছরের একজন মেয়ে দৌড়ে এসে বললো,” খালা দেহেন,আমাইগে ধারে একটা গরু ঢুকছে।” আমি বললাম বলিস কী? চল্চল্ দেখে আসি। আমি গিয়ে দেখি একটা বড়সড় বিড়াল। পাসের কোনো স্টাফের হয়তো হবে,ড্রেনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত বিড়াল ঢুকবার সুযোগও জেলখানায় নেই। আমি বুলুর দিকে তাকিয়ে বললাম, এই তোর গরু? সে সময় সেই বিড়াল নিয়ে লেগে গেলো এক হুলস্থুল কাণ্ড। কীভাবে এলো। ড্রেনের মুখে শিক দেওয়া আছে। ঐ শিক দিয়ে যেভাবেই হোক বিড়ালটা ঢুকে পড়েছে। যাইহোক আমি বুলুকে জিজ্ঞাসা করলাম তুই বিড়াল চিনিস? ও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক’রে তাকিয়ে থাকলো। ও হয়তো বিড়াল গ্রু এই শব্দগুলো শুনেছে। কিন্তু না দেখার জন্য পার্থক্যটা বোঝে না। বুলু যখন পেটে তখন ওর মা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে সেই যে জেলে ঢুকেছে আর বেরোইনি। এই সমস্ত বাচ্চারা বড় হলে তবে অভিভাবক বদলানো হয়। আমি এবার বুলুর কাছে জানতে চাইলাম এই যে মাংস খেতে দেয়, সে কোথায় পাওয়া যায়? মাসে একবার মাংসের নামে ছোট ছোট দুই একটা টুকরো ওরা খেতে পায়। বুলুর কাছে যখন মাংসের কথা জানতে চাইলাম,ও নির্বিকার ভাবে বললো ক্যান্,পুকুর থেইক্যা আহে। বুলুর মা এভাবেই কথা বলতো। আমি বুলুর কথা শুনে তো হা হয়ে গেলাম। ভাব্লাম বলে কী! বুলু মনে হয় ওর মায়ের কাছে পুকুরের গল্প শুনেছে। কারণ মধ্যে মধ্যে ওদের মাছও খেতে দেওয়া হোতো। পাখী বলতে ওরা কাকই চিনতো। জেলের মধ্যে শুধু কাকই আসতো। আমি অবশ্য সন্ধ্যার দিকে গেটের কাছে একটা গাছে চড়ুই পাখির কিচির মিচির শুনতাম। সেল থেকে তা দেখাও যেতো। বচ্চারা তখন থাকতো তালা বন্ধ অবস্থায়। ওদের চড়ুই পাখি তাই আর
হোতো না। দিনের বেলায় ওয়ার্ডের মধ্যে কোনো পাখ পাখালি দেখতাম না। সম্ভবত আকশে উড়তে পারা পাখিও চার দেয়াল পছন্দ করতো না। কারাগারের মধ্যে এভাবেই অনেকটা বন্য প্রাণীর মতো বেড়ে উঠছিলো কিছু মানব শিশু। ওরা এমনই অভাগা,প্রকৃতির সঙ্গেও ওদের কোনো পরিচয় ছিলো না। কেউ ওদের খোঁজ নেয় নি,কেউ ওদের খোঁজ করেনি। তবে একথা বলা যায় ওরাই এখন আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ।
আমি বলেছি,বাড়ির সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ ক’রে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে এটা ছিলো আমার জন্য শাস্তি। কারাগারের ভিতরে সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে আমাকে ক’রে দেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্ন। জেল কতৃপক্ষ আমাকে এই শাস্তি দিয়েছিল। নিজের টাকায় ইত্তেফাক পত্রিকা কিনে পড়তাম। জেল গেট থেকে আমাকে জানানো উচিৎ নয় মনে করলে,সে খবরের উপর কালী দিয়ে দেওয়া হোতো। এখন আমার একমাত্র সঙ্গী বাচ্চারা। সকালে বিকালে মেট্রন আমার সঙ্গে বসেই চা খান। তখন তার সঙ্গে কিছু ভালো মন্দ কথা হয়। আর আছে আমার সব সময়ের সঙ্গী মাজেদা। মাজেদা আবার উত্তর দেওয়া ছাড়া নিজে থেকে কোনো কথা বলতো না।
ঠিক এই সময়েই পেলাম নতুন বার্তা। সুবেদার সাহেব বিকালে জানিয়ে গেলেন, কাল আপনার জেল ট্র্যান্সফার। সকালে যেতে হবে। তৈরি থাকবেন। তবে আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে,তা বলা হোলো না। শুধু বললেন,তৈরি থাকবেন। পরদিন সকালে যখন আমার বিদায়ের সময় হয়ে এলো, আমি মাজেদাকে কোথাও দেখলাম না। কোথায় বসে হয়তো কাঁদছে। বাপ্পি চলে যাওয়ার পর রুশিয়া নামে একজন মেয়ের কাছে আমি গান শুনতাম। বিধিনিষেধের মধ্যেও রুশিয়া লুকিয়ে আমাকে দেখতে আসতো। সেই রুশিয়াও কোথায় যেন লুকিয়েছে। অন্য মেয়েরা তো কষ্টে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। এতদিন তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি, এ তাদের অনেক বড় কষ্ট। আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম,কাজ তো হয়েছে। পানির সমস্যার সমধান হয়েছে। এটা গল্প করতে পারার থেকেও বড়। কনক আমার সামান্য জিনিসপত্র সেল থেকে গুছিয়ে নিয়ে এলো। এরপর মেট্রন এবং একজন জমাদ্দার আমাকে জেল গেটে নিয়ে গেলো। জেলগেটে জেলর সাহেব ছিলেন। গেটের বাইরে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ স্কট অপেক্ষা করছে। জেল গেট থেকেই আমাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হোলো। এরপর সেই আগের মতোই মাঝে একটা গাড়িতে আমি এবং সামনে পিছনে পুলিশ বহর আমাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। এবারও আমার মা জানতে পারলো না আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাকে অন্ধকারে রেখেই পুলিশ বাহিনী আমাকে নিয়ে ছুটে চললো নতুন গন্তব্যে।
# চলবে
– তাহেরা বেগম জলি, সাবেক শিক্ষিকা, রাজনৈতিক কর্মী